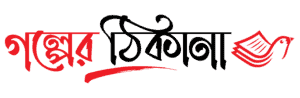#একজন সেরাদের সেরা লেখক : Afia Afrin
গল্প:ভালোবাসা বৃত্তান্ত
১
তানিয়াপু ছিলেন, যাকে বলে ‘সেন্টার পিস অফ শো-কেইস’ অথবা, ‘চেরি অন দ্যা কেক’—তাই-ই। মহল্লার ছেলেরা অবশ্য এত ভাল ভাল নামে ওকে ডাকত না—মানে আড়ালে-আবডালে ওকে নিয়ে যখন আলাপ করত আর কী! যা সব নাম ধরে ডাকা হতো—সেগুলো শ্রাব্য-ও নয়, কথ্য-ও নয়; আর লেখ্য তো নয়-ই! সেদিকে আর না যাই। তারচেয়ে, একেবারে গোড়া থেকেই বলি বরং।
আমাদের ৩৩/৩, গোলবাগ স্কুলপাড়ার লাল রঙা পাঁচতলা বাড়িটাতে তানিয়াপুরা উঠেছিলেন এক ঝুম বৃষ্টির দুপুরে। সেদিনই ওর সবচেয়ে সুন্দর এবং শ্রাব্য নামটি দিয়েছিলেন মহল্লার বিশিষ্ট কবি আরিফ ভাই—“বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল”। কদমরঙা নরম হলুদ জামা পরে, কদমের ডাঁটির মতোই সরু পা’জোড়া গাঢ় সবুজ রঙা চুড়িদারে মুড়িয়ে ছুটোছুটি করা মেয়েটির এহেন নামকরণ যথাযথ রকমেই সার্থক ছিল। ওকে যখন প্রথম দেখি—দুই হাতে দুই গোলাপের চারা বসানো টব নিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। ট্রাক থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত আসতে আসতে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে একদম, কব্জি অবধি ঝোলানো বিনুনি বেয়ে টুপটাপ ঝরছে শিশিরের মতোন বৃষ্টির পানি। আমরা তখন চার তলাতে থাকি, বাসা বদল করে ওরা উঠেছিল ঠিক নিচেই—তিন তলাটায়। বৃষ্টি এলে স্কুল মাঠে ফুটবল খেলাটা আমাদের নেশা, সৈকতটা তো পরে এটাকেই পেশা বানিয়ে নিয়েছিল—জাতীয় দলে নাম লেখিয়ে নিয়ে। সে যাই হোক, আব্বার কিনে দেওয়া নতুন ফুটবলটা আঙুলের মাথার ঘোরাতে ঘোরাতে মনের আনন্দে সিঁড়ি বেয়ে নামছিলাম আমি, আর বাদলের কদম হয়ে তানিয়াপু উঠছিল দুদ্দাড় করে—সেই একই সিঁড়ি বেয়ে।
কী ভাবছেন? নাটক-সিনেমার মতোন প্রথম দেখাতেই নায়ক-নায়িকার ধাক্কা? ধুর! অত আগ বাড়িয়ে ভাবতে যান কেন বলুন তো? ধাক্কা-টাক্কা খাইনি, এমনকি একটু ‘টাচ’-ও নয় (বলা বাহুল্য, এই নিয়ে বিস্তর রকমের আফসোস করেছি পরে)। কেবল ওরকম পরীর মতোন ভয়ংকর সুন্দর একজনকে আকস্মিক চোখের সামনে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিলাম, আঙুলের মাথা থেকে ব্যালেন্স হারিয়ে টুপ করে পড়ে গিয়েছিল হাতে ধরা ফুটবলটা। সিঁড়ি বেয়ে স্লো-মোশনে নায়ক-নায়িকা নয়, ধুপুস-ধাপুস করতে করতে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল আমার সাধের বলটা!
সেই শুরু! এরপর টপাটপ, টপাটপ গড়িয়ে পড়তে লাগল—না, ফুটবল নয়; ফুটবল প্লেয়াররা! বত্রিশ নাম্বারের সবচেয়ে ষণ্ডামার্কা জহির ভাই, যার নাম শুনলে মহল্লার পুরনো কাকেরা পর্যন্ত ‘কা কা’ করা থামিয়ে দেয়—স্বয়ং তিনি এসে ধর্ণা দিলেন আমার কাছে। এই পনের বছরের একটুখানি, লিকলিকে আমি—বডিবিল্ডার জহির ভাইয়ের এক ফোঁটা ফুঁ-তে উড়ে গিয়ে সোজা মিতুলদের ছাদে মুখ থুবড়ে পড়ব—সেই আমার কাছে কিনা জহির ভাই এলেন মুখ কাঁচুমাঁচু করে!
“শুনলাম, এলাকার বিচ্ছু পোলাপান প্যাকাটি বলে নাকি তোকে ক্ষ্যাপায়? তুই কিচ্ছু চিন্তা করিস না, সবগুলিকে দেখে নেব একদম! আজকে থেকে মনে কর—আমি তোর বডিগার্ড। তোর বন্ধু মানে আমার বন্ধু, তোর শত্রু মানে আমারও—তুই খালি আমার একটা কাজ করে দে, ভাই!”
ব্যক্তিগত ডাকপিয়ন হিসেবে সেই আমার প্রথম নিয়োগপ্রাপ্তি। নীল রঙের খামের ভেতর লাল রঙের কাগজে জহির ভাইয়ের কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং মার্কা হস্তাক্ষরে লেখা চিঠিটা আমার হাত হয়েই তানিয়াপুর হাতে পৌঁছেছিল।
তানিয়াপুদের ঠিক মাথার ওপরের তলাতেই থাকবার সুবাদে এরপর তানিয়াপুর আরও অসংখ্য পাণিপ্রার্থী তেলতেলে মুখ করে আমার পাণি প্রার্থনা করেছে; আমার হাতখানা ছাড়া তানিয়াপুর কাছে চিঠি পৌঁছুবার আর কোনো উপায় ছিল না কিনা! যখনকার কথা বলছি, তখন এমন হাতে হাতে সেলফোন ছিল না, ইন্টারনেটের তো নামই শোনেনি কেউ! আমি তখন সবে ক্লাস এইটে উঠেছি, অর্থাৎ একানব্বই কি বিরানব্বই সালের কথা এসব।
তানিয়াপুর বাবা ছিলেন পুলিশের আই.জি নাকি অ্যাডিশনাল আই.জি—কী যেন, ঠিক মনে নেই, তবে খুব বড়সড় পদ—এটুকু মনে আছে। ঝামেলাহীন সংসারে জনা তিনেক প্রাণী, তানিয়াপু আর ওর মা-বাবা। আমারই ভাগ্য বলতে হবে, তানিয়াপুর কোনো ছোট ভাই-টাই ছিল না। অতএব, তানিয়া নামক অধরা চাঁদটির কাছে পৌঁছবার জন্য এলাকার বড় ভাইরূপী সমস্ত বামনের কাছে আমি ছিলাম এক এবং একমাত্র বাহন। মিথ্যে বলব না, বাহন হিসেবে আমি ছিলাম নিতান্তই অপদার্থ এবং লোভী। পড়া তো দূরের কথা, চিঠিগুলি খুলে অবধি দেখত না তানিয়াপু। আমার চোখের সামনেই খামসহ কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিত। তবে এসব খবর ও-প্রান্তে পৌঁছত না। মনের মাধুরী মিশিয়ে যা হোক দু’একটা শব্দ লেখে-টেখে যথাযথ প্রাপককে চিঠির উত্তর দেওয়ার কাজটি আমি বিনা পারিশ্রমিকে এবং নিজ গরজেই করতাম।
সুযোগ পেলে কে না তার সদ্ব্যবহার করে? বামনদের বাহন হলেও নিতান্ত জড়বস্তুটি তো আর নই, তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে আমিও ছাড় দিলাম না। চিঠিপ্রতি দুই টাকা করে নিলেও মাস শেষে হেসেখেলে তিরিশ-চল্লিশ টাকা উঠে যেত। চার আনায় হজমি চকলেট, আট আনায় ‘আইসক্রিম’ নামধারী পলিথিন মোড়ানো কমলা-সবুজ রঙের বরফের স্টিক (আম্মা-আব্বার ভাষ্যমতে, যেগুলি কী না ড্রেনের পানি দিয়ে বানানো ছিল) আর ভাঙ্গারি জিনিসে কটকটি খাওয়ার আমলে ঐ তিরিশটি টাকার মূল্যমান ঠিক কতখানি ব্যাপক ছিল— এ যুগে বসে সে আমি বলে বোঝাতে পারব না, সে বৃথা চেষ্টাটি করছিও না। তানিয়াপুর কল্যাণেই আমি আঙুল ফুলে একরকম কলা গাছ হতে আরম্ভ করলাম। টংকার ঝংকারে সেই কংকালসার ‘প্যাকাটি’ আমিও বন্ধুদের কাছে বেশ একটা মর্যাদার আসন বাগিয়ে নিলাম। রবিনের বাবা রোজ ওকে হাতখরচা দিতেন বলে বেশ একটা দেমাগ ছিল ওর। আমার এহেন দিলখোলা খরচা দেখে বেশ করে ঈর্ষান্বিত নজর লাগিয়ে সে ফোঁসফোঁস করে বলে বেড়াতে লাগল, “প্যাকাটিটার কপাল দেখ! ওর হাড্ডিগুড্ডির নিচেই কি না তানিয়াপুরা এসে উঠল? শালার শরীরে মাংস না থাকলে কী হবে, কপালটা নিয়ে এসেছে এত্ত বড়!”
হিংসুক রবিনের মুখে ছাই দিয়ে দোয়েল পাখির ছাপ বসানো দুই টাকার নোট নামক ‘ম্যাজিক কার্পেটে’ করে আমি হাওয়ায় উড়তে আরম্ভ করলাম। কথায় বলে, পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে। আমার পাখা গজানো থেকে আরম্ভ করে এই ‘মরা-মরি’ পর্যন্ত সময় ছিল মাত্র পাঁচ মাস।
পনেরর ঘর ছেড়ে ষোলতে পা দিতে দিতে আমিও মরলাম। এই মরণ সেই মরণ নয়। এই মরণ সেই মরণ—যে মরণে মরলে লোকে জলে ডোবে না।
আমি তানিয়াপু নামক পরীটির প্রেমের জলে ডুবে মরলাম।
২
তিন বোনের পর আমি এক ভাই। বাড়িতে আমার অসম্ভব আদর, অতি আদরে কিছুটা বাঁদর হয়েছি—একথাও অনস্বীকার্য। আদরের বাহুল্যে আম্মা এবং আপারা মিলে প্রতি বছর খুব ঘটা করে আমার জন্মদিন করতেন। শৈশবের আনন্দময় এই অনুষ্ঠানটি কৈশোরে এসে আমার দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আম্মা নিজে বাড়ি বাড়ি যেয়ে আমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করে আসতেন। ভাঙা বদনা কিংবা একপাটি ছেঁড়া স্যান্ডেলকে র্যাপিং পেপারে মুড়ে দাঁত কেলাতে কেলাতে জন্মদিনের ভোজ খেতে হাজির হতো অসভ্য, বর্বরের দল। বড় আপা প্রত্যেকবার নিজের হাতে কাগজের টুপি বানাতেন, চুলোয় বালি চাপিয়ে মেজ আপা বানাতেন ইয়া বড় বার্থডেকেক আর ছোটপা ছিলেন ডেকোরেশনের দায়িত্বে। বাদবাকি সবকিছু—আম্মার ডিপার্টমেন্ট। বাঁদর হলেও আমি বরাবর নরম মনের মানুষ, ওদের এই ‘নিরঙ্কুশ আনন্দে’ ব্যঘাত ঘটাতে মন সায় দিত না। তাই প্রতি বছর জানুয়ারির পঁচিশের মতোন সেবারও সারাদিনব্যাপী ভীষণ আপত্তি-টাপত্তি শেষে আমাকে দেখা গেল—মিকি মাউজ আঁকা কাগজের টুপি মাথায়, হার্ট শেপের বিশাল কেকের সামনে, গাদাখানেক বেলুন আর কর্ক-শিটে তৈরী আজগুবি আকারের সব ঝুলন্ত বস্তুর নিচে, গোমড়ামুখ করে বসে আছি বসার ঘরের সেন্টার টেবিলটার সামনে। কে জানত, এবারে বড় আপা নাচতে নাচতে যেয়ে তানিয়াপুকেও দাওয়াত করে আসবে?
অবিনাশ আর মিতুল বাদে অন্য কেউ তখনও আসেনি। এই দু’টো বরাবরের পেটুক, দাওয়াত পেলে সকাল থেকে দাঁত মাজতে আরম্ভ করে দেয়। বড় আপার বানানো সঙের টুপিটাকে নিয়ে লোফালুফি করছিল দু’জনে মিলে, দরজার ওপাশ থেকে মনে হলো—একরাশ আলো ঝলকে এলো।
তানিয়াপু!
তানিয়াপুর তখন দশম শ্রেণী। ওল্ড টেন—মানে আর কিছুদিন পরেই ম্যাট্রিক দেবেন। আর আমার সবে ক্লাস নাইনের শুরু। মাঘের বাঘ কাঁপানো শীতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, বয়সের ব্যবধানকে তুচ্ছজ্ঞান করে আমি তানিয়াপুর প্রেমে পা হড়কে পড়লাম। তানিয়াপু, কে বলেছিল তোমায় সেদিন শাড়ি পরে আসতে? কে?
“হ্যাঁ রে প্যাকা! তোদের দরজার ঐ পাশে স্বর্গ নাকি রে? টুপটাপ অপ্সরা ঝরে ঝরে পড়ে—”, অবিনাশ সাহা ঢোঁক গিলে বলল। মিতুল তখনও হাঁ করে আছে।
প্রেমের মরা জলে ডোবে না। ভীষণরকম ডুবে গিয়েও আমি তাই ভেসে রইলাম। মুখে চরম গাম্ভীর্য এনে বললাম, “দিদি হয় তোর! সাবধানে কথা বলিস!”
“দিদি নয়, বৌদি! অবিনাশের বৌদি, তোর ভাবী আর আমার বউ—”, মিতুল মুখ খুলল তারপর।
মিতুলের হাতে ধরা পেপার ক্যাপটা ছোঁ মেরে নিয়ে ওটা দিয়েই ঝপাং করে চড় বসিয়ে দিলাম ওর গালে।
“বড়দের নিয়ে ইয়ে করতে ইয়ে লাগে না তোর? হ্যাঁ?”
‘ইয়ে’র দাপটে মিতুল চুপসে গেলেও, আমার নিজেকে আচমকা খুব বড় মনে হতে লাগল। ইতোমধ্যে এর-ওর-তার হয়ে পিয়নগিরি করতে গিয়ে তানিয়াপুর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা হয়ে গিয়েছিল আমার। নানাজনের চিঠির জবাব দিতে গিয়ে আমাকে বহু তথ্য যোগাড় করতে হয়েছে, যেমন—তানিয়াপুর জন্মদিন, প্রিয় খাবার, প্রিয় ফুল, প্রিয় বই, প্রিয় লেখক ইত্যাদি ইত্যাদি। তিন বোনের শেষে নিতান্ত সরল চেহারার গোবেচারা ভাইটি ছিলাম বলে তানিয়াপু আমায় স্নেহের চোখেই দেখত। সেই ‘স্নেহাস্ত্র’টিকেই কাজে লাগিয়ে আমি তথ্য পাচারকার্যে লিপ্ত হয়েছিলাম অবলীলায়। এবারে দাবার চাল গেল উল্টে—কোচ নামল খেলতে, ড্রাগ ডিলার নিজেই ধরল ড্রাগ। একে-ওকে-তাকে ঝটপট ‘প্রেম বিষয়ে আগ্রহী নই’- বার্তাটি জানিয়ে দিয়ে আমি ফাঁকা মাঠে গোল করবার প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম। ফাঁকতালে নিজেকে ভারিক্কি দেখাবার জন্যে আরও দু’টো কাজ করলাম—
এক, গোঁফ-দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিলাম।
দুই, সকলের অজান্তে সিগারেটে ঠোঁট পোড়াতে আরম্ভ করলাম।
সেই সময় আমার সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সময়ে-অসময়ে তাঁর ‘যৌবনের গান’ প্রবন্ধের বিশেষ বিশেষ অংশ আমি তানিয়াপুকে পড়ে শোনাতে লাগলাম। সেই বিধ্বংসী মাঘের শেষদিকে, এক কুয়াশা পড়া বিকেলে তানিয়াপুকে পাকড়াও করে বললাম, “ ‘বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বেঁধে রাখা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি- যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যর মতো প্রদীপ্ত যৌবন।’—এই অংশটার সারমর্ম করে দাও!”
নিঁখুত ছাঁচে ঢালা ভ্রূ জোড়ায় বিস্ময় মেখে তানিয়াপু বলল, “মাত্র তো তিনটা লাইন! এর আবার সারমর্ম কী?”
“আহা! দাও না!”
“আরে, মানে হলো—বয়স দিয়ে জোয়ান-বুড়ো বাছবিচার করা যায় না। এই তো, আর কী?”
আমার তখন মুখভর্তি বিরহের দাড়িগোঁফ, বুকপকেটে আধখাওয়া সিগারেটের টুকরো। তানিয়ার গভীর, কালো পাপড়ি বসানো টলটলে চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে আমি বললাম, “তারমানে— মনের বয়সই আসল বয়স, বার্থ সার্টিফিকেটেরটা নয়। তাই তো?”
“হুঁউ! ওরকমই—”
“চিঠি দিলে ছিঁড়ে ফেলে দেবে, ও পথে তাই যাব না। এই জন্মদিনে আমার একবারে তিন বছর বয়স বেড়ে গেছে। মনের বয়সে এখন আমি তোমার থেকে পাক্কা এক বছরের বড়। তাই নাম ধরেই বলছি—তানিয়া, আমি তোমাকে ভালবাসি!”
শীতের ছোট্ট বিকেলটা তখন জীবন সায়াহ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার ঐ হাস্যকর স্পর্ধা দেখে এক মুহূর্তের জন্য সে-ও যেন খানিক থমকে দাঁড়ালো। ঝুপ করে সন্ধ্যা নামবার আগে বিকেলের শেষ আলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মেঘেদের গলা ধরে ঝুলে রইল অনেকটা ক্ষণ। তানিয়ার বিস্মিত চোখের তারায় সেই আলোর নাচন, আমি তখনও সেই চোখে চেয়ে আছি স্থির।
“এত পেকে গেছিস, তোর বড়পাকে বলে দিলে কেমন হবে রে পাজি?”, ফট করে আমার ডান কানটা টেনে ধরে মাথাটাকে ভীষণরকমে ঝাঁকিয়ে দিলো তানিয়াপু—যেমনি করে স্কুলগেটের সামনে দাঁড়িয়ে মুড়িমাখা ঝাঁকান কাশেম মামা।
আমি তখনও নিজের গাম্ভীর্য ধরে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি। এক ঝটকায় কানটাকে মুক্ত করে, গলাটাকে যথাসম্ভব ভারী করে নিয়ে বললাম, “আমি সত্যিই বলছি। দুই বছর তো মাত্র ডিফারেন্স, তাতে আবার এত কী? তুমি যখন মাস্টার্স করবে, আমি তখন অনার্স শেষ করেই একটা চাকরিতে ঢুকে যাব। ততদিন কেবল অপেক্ষা করবে, বলো? কথা দাও?”
কথাগুলি এখন যতটা ছেলেমানুষি শোনাচ্ছে, তখন কিন্তু তেমন শোনায়নি! বুকের ভেতর তখন আমার দ্রিমদ্রিম রণঢাক বাজছে, রাতজাগা রক্তাভ চোখে আমি ঠায় চেয়ে আছি তানিয়াপুর দিকে। চিরন্তন যে শীতের বিকেল, বহুকালের অভিজ্ঞতায় সে ঠিক বুঝেছিল—কী ভীষণরকম হাস্যকর একখানা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে ৩৩/৩, গোলবাগ স্কুলপাড়ার এই বাড়িটার ছাদের ওপর। খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়েই ঠা-ঠা করে হেসে আবার চলতি পথ ধরেছিল সেই বিকেলটা। অন্ধকারের কালো চাদর ধীরে ধীরে নেমে এসেছিল ছাদের কার্নিশ বেয়ে। স্পষ্ট দেখলাম—সেই অন্ধকার ছায়া ফেলেছে তানিয়াপুর নিদারুণ সুন্দর মুখখানার ওপরেও।
অন্ধকার গাঢ় হবার আগেই তানিয়াপু চলে গেলেন। যাবার আগে কেবল বলে গেলেন, “মুহিব, তুই আর আমার ধারে-কাছেও আসবি না। পড়া বুঝতেও নয়, কারো চিঠি দিতেও নয়—কোনো কিছুর জন্যেই নয়। মনে থাকে যেন!”
তারপর নামলো সন্ধ্যা। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। রাত পেরিয়ে গভীর রাত। আমার মনে হলো, পৃথিবীর সমস্ত কষ্ট, সমস্ত অপমান—অন্ধকারের রূপ ধরে আমার উপর হামলে পড়ল। ঐ একই জায়গাতে, একইভাবে আমি বসে রইলাম জড় পাথরখন্ডের মতোন। রাতের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ল শীতের তেজ, মশাদের দল মহানন্দে ঘের দিয়ে ধরল আমার প্রস্তরবৎ শরীরটাকে, উত্তরের বাতাসে জমে গেল কানের লতি—আমি তবু উঠে যাবার স্পৃহাটুকু খুঁজে পেলাম না।
ওদিকে আম্মা আর আমার তিন বোন মিলে বাড়ি বাড়ি যেয়ে আমাকে খুঁজে মরছেন। তারা জানেন, খেলতে গিয়ে আমি উধাও হয়েছি। তানিয়াপুদের বাসার খোঁজ করার কথা তাদের মনে পড়ল মাঝরাতে গিয়ে। ততক্ষণে আব্বা মসজিদের দিকে রওনা করেছেন—মাইকিং করতে, আম্মা বার দু’য়েক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। বড় আপার অবস্থা দেখে তানিয়াপু ভেবেছিলেন আমি বোধহয় বাসা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছি কোথাও। “মুহিব তো ছাদে ছিল আমার সাথে, বিকাল বেলায়—”, বলতে বলতে একছুটে দৌড়ে এসেছিলেন ছাদে। তার পেছন পেছন বড় আপাও।
প্রথম যে চড়টা আমার গালে পড়েছিল, সেটা তানিয়াপুর। আমার তখন আউলঝাউল মাথা। প্রথম প্রেমের প্রচণ্ড দহনে বিশ্বজগতের সমস্ত কিছুকে নিতান্ত বালখিল্য, তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। কে আম্মা? কে আব্বা? কে বড়পা?—এদের কাউকে আমার তখন দরকার নেই। তানিয়াপু চড় মেরেছিল বামপাশের গালে, সেই পাশটাকে আমি পরম আদরে আঁকড়ে ধরে রইলাম। এরপর বড়পা আর আব্বার হাতে চড় খেয়েছিলাম সেদিন, দুটোই ডানপাশের গালে। বহুদিন বাম গালে আমি কাউকে ছুঁতে দেইনি। ‘ভালোবাসি’ বলবার আগে তানিয়াপু বহুবার আমাকে ছুঁয়েছে। কিন্তু, ‘ভালোবাসি’ বলবার পর তানিয়াপু…না, তানিয়ার স্পর্শ পাওয়া আমার সেই প্রথম। ওর ঐ “ধারে-কাছে না ঘেঁষবার” কঠিন শর্তের কারণে আমি ধরেই নিয়েছিলাম, এই প্রথম পাওনাটুকুই আমার শেষ পাওনাও বটে।
কিন্তু ভাগ্যের কথা কে কবে জানতে পেরেছে?
৩
তানিয়াপু তখন কলেজের ছাত্রী, আমি বিরহে দেবদাস হয়ে লেখাপড়া প্রায় ভুলতে বসেছি। খুব বেশি দিন নয়, মাত্র চার কি পাঁচ মাস পরের কথাই বলছি। আগে আম্মার সাথে একরকম মারামারি করেই প্রতিদিন খেলতে যেতে হতো আমার। ইদানিং পাশার দান উল্টে গেছে। আম্মা আর আপারা মিলে আমাকে রীতিমত জোরাজুরি করে খেলতে পাঠান। মাঠের বদলে আমি ছাদে গিয়ে বসে থাকি চুপচাপ। বিকেল গড়ালে আবার ঘরে ঢুকে যাই।
সেদিনও তেমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম ছাদের ওপর।
তানিয়াপু আর মেজ আপা মিলে কলেজ থেকে ফিরছিলো, একই কলেজে পড়ে ওরা দু’জনে। একটা অনুভূতিহীন গোল আলুর মতোন চোখ করে আমি দেখছিলাম ওকে—কাঁধের দুইপাশে ঝোলানো লম্বা বিনুনি, ক্রস করে দেওয়া ধবধবে সাদা ওড়নাটার আড়ালে তানিয়াপুর অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য, ওর ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটবার সুন্দর ভঙ্গিটা—
আরও একজোড়া শকুনচোখ-ও যে ওর দিকে দৃষ্টি পেতে বসে ছিল—আমি টের পাইনি। তানিয়াপুও নয়। ঘটনাটা ঘটলো তাই একেবারে আকস্মিক ভাবে। মেজ আপা ছিলেন ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরিটার কাউন্টারে। ভিড় এড়াতে তানিয়াপু দাঁড়িয়ে ছিলেন একটু দূরে—মুখে কাপড় বাঁধা ছেলেটা ওর দিকে দৌড়ে এলো ঠিক তখনই, কী যেন একটা ছুঁড়ে দিয়ে গেল তানিয়াপুর চোখেমুখে। তারপর, কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত… তানিয়াপুর প্রচণ্ড চিৎকারে জগত সংসার কেঁপে উঠলো। দৌড়ে আসা ছেলেটার পরনের গোলগলা গেঞ্জিটা আমার চেনা। ছত্রিশের লাইনের রিপনভাই। এর আগে বহুবার তানিয়াপুকে চিঠি দিয়েছে সে, তানিয়াপুর হয়ে আমিও উত্তর দিয়েছি ওকে—চিঠিপ্রতি দুই টাকার বিনিময়ে।
এরপর, ঠিক দেড়দিন পর, তানিয়াপুকে আমি দেখলাম গোলবাগ সরকারি হাসপাতালের এক কামরার কেবিনে। মুখের একপাশ আর গলা জুড়ে সাদা ব্যান্ডেজ। সেই দেড়দিনে বইপত্র ঘেঁটে আর লোকের মুখে মুখে আমি জেনে গিয়েছিলাম, অ্যাসিড জিনিসটা কী প্রচণ্ড ভয়ংকর। একবার ছুঁয়ে দিলে আজীবন দাগ থেকে যায়…
তানিয়াপু আমাকে দেখে সামান্য হেসেছিল। ওর ঐ অসম্ভব সুন্দর হাতটা দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছিল আমার হাত। ফিসফিস করে বলেছিল, “রিপন আমাকে কিছুদিন ধরে খুব জ্বালাচ্ছিল, জানিস মুহিব? শুধু বলতো-‘প্রেম যখন করবেই না, এতদিন ধরে আমার চিঠির উত্তর দিলে কেন? সবাই জানে তোমার সাথে আমার চলে—’। কেন বলতো এমন? আমি তো ওর কোনো চিঠির কোনো উত্তর দিইনি, কী চিঠি দিয়েছিল সেটাও পড়িনি…ওর কেন এত রাগ ছিল তবু আমার ওপর—”
এক জন্মদিনে আমার বয়স বেড়েছিল তিন বছর। তানিয়াপুর এই এক প্রশ্নে আমি এক লাফে আবার সেই আগের মুহিব হয়ে গেলাম—ভীতু মুহিব, প্যাকাটি মুহিব। রিপনভাইকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ, জেরার মুখে ও যদি বলে দেয় চিঠির কথা…সেই কথা ধরে ফেঁসে যাব আমি! আমাকেও হাজতে পুরে দেবে!
আউলা প্রেমের বাউলা বাতাস তখন আমার মাথা থেকে উধাও। হাজতে যাবার তীব্র ভয়ে ভেউভেউ করে কাঁদছি। আম্মা আর মেজআপা ভাবছেন আমি তানিয়াপুর জন্য কাঁদি, তারাও কাঁদছেন।
ঠিক তখনই তানিয়াপু আমায় দ্বিতীয়বারের মতো ছুঁয়ে দিলেন। চোখের পানি মুছিয়ে দিতে দিতে ফিসফিস করে বললেন, “কাঁদিস না মুহিব। আমার হয়ে রিপনকে কে উত্তর দিতো সেটা আমি আর তুই ছাড়া আর কেউ জানবে না। আই প্রমিজ!”
তানিয়াপু কথা রেখেছিলেন। সকলের প্রশ্ন আর ধিক্কারের তীর বুকে আগলে নিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে গেছেন চুপচাপ, হাসিমুখে। এই ঘটনার পর ওরা আমাদের মহল্লায় ছিলেন মাত্র এক মাসের মতোন। আঙ্কেল, মানে তানিয়াপুর আব্বা চেষ্টাচরিত্র করে মাসখানেকের মধ্যেই পোস্টিং নিয়ে যশোরে, ওদের গ্রামের বাড়ির কাছাকাছি চলে যান। যাবার আগের দিন বিকেলে তানিয়াপুর সাথে আমার শেষবার দেখা হয়েছিল। ওর সেই অসম্ভব রকমের মিষ্টি হাসিটা তখন ধ্বংস হয়ে গেছে পুরোপুরিভাবে। তবু হেসে হেসেই জিজ্ঞেস করেছিল, “এখন আর চিঠি আসে না আমার নামে। না রে মুহিব?”
আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, মেঝের দিকে তাকিয়ে। কেমন করে বলব, যে আরিফ ভাই তোমাকে ‘বাদল দিনের কদম’ নাম দিয়েছিল, আজকাল সে নাকি তোমাকে দেখলে রাতের বেলায় দুঃস্বপ্ন দেখে। মিঠুনভাই তোমাকে এক নজর দেখবে বলে কলেজ ফাঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ঐ বকুল গাছের নিচে প্রত্যেকদিন দুপুরে, সে আজকাল মেজ আপাকে প্রেম নিবেদন করে বেড়াচ্ছে। “তোমাকে না পেলে মরে যাব”—চিঠিতে লেখেছিল রোকনভাই। সে যে কেবল দিব্যি হেসেখেলে বেঁচে আছে তাই-ই নয়, এর-ওর কাছে বলে বেড়াচ্ছে, “রূপের অত দেমাগ থাকলে না, এমনই হয়! ধরাকে সরা জ্ঞান করতো ঐ রূপের দাপটে, হলো না এবারে?”
এসব আমি বলতে পারি না। আমি তাই মেঝের দিকে তাকিয়ে রই চুপচাপ।
“মুহিব! আমাকে তুই অপেক্ষা করতে বলেছিলি, মনে আছে? যদি বলি আমি অপেক্ষা করব—তুই আসবি?”, তানিয়াপু আচমকা জিজ্ঞেস করেন। স্থির, শান্ত গলায়।
আমার বুকের ভেতরটায় কাঁপুনি দিয়ে ওঠে। সেই মাঘ মাসের শীতের রাতে খোলা ছাদে বসে থেকেও এই হাড়কাঁপানো অনুভূতির সন্ধান আমি পাইনি। হতভম্ব আমি তানিয়াপুকে দেখে শিউরে উঠি। মুখের একপাশ যেন গলে গেছে একদম, পদ্মফুলের পাপড়ির মতো যে ঠোঁটটার ওপর মনে মনে হাজার-একবার ঠোঁট ছুঁইয়েছি—গালের চামড়ার সাথে গলে মিশে গেছে একদম সেই ঠোঁটের একপাশ। নিঁখুত ছাঁচে বানানো পানপাতার মতোন মুখটা এখন সামঞ্জস্যহীন—একদিক রয়ে গেছে আগের আদলেই, অন্যদিক থেঁতলানো মাংসের মতোন পচে-গলে গেছে একদম! যে মুখটা এক নজর দেখলে বিশ্বজগত তুচ্ছ মনে হতো, আজ সেই মুখে দিকে তাকাতেই অন্তরাত্মা পালাই, পালাই করছে কেন? ভালবাসা কি তবে এতটাই স্বার্থপর? এতটাই মেকি?
হায় খোদা! এই তানিয়াপু আমার জন্য অপেক্ষা না করুক! কারো জন্য অপেক্ষা না করুক!
৪
তানিয়াপুর সাথে সেই আমার শেষ দেখা। তারপর বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেকটুকু পানি গড়িয়েছে। ষোল বছরের সেই মুহিব তিরিশের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।
এই নাতিদীর্ঘ জীবনপথটুকুতে আরও নতুন দু’জন সঙ্গী জুটেছে আমার—স্ত্রী ফারহানা আর পাঁচ বছুরে পুত্রসন্তান ফাইয়াজ। নয়টা-পাঁচটার সরকারি চাকুরে আমি তানিয়াপুর কথা একরকম ভুলেই গিয়েছি। কেবল হঠাৎ হঠাৎ টেলিভিশন কিংবা পেপারে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা দেখলে তানিয়াপুর আধগলা মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আশ্চর্যের বিষয়, যে তানিয়াপুকে এককালে ভালবেসেছিলাম, তার পদ্মদীঘির মতোন শান্ত, সুন্দর চেহারাটা হাজার চেষ্টাতেও মনে করতে পারি না আমি আর!
পৃথিবী গোল হলেও, অত্যন্ত বিশাল। তাই এক জীবনে হারিয়ে ফেলা মানুষদের আবার খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বড়ই ক্ষীণ। কিন্তু, জীবন বড় রহস্যময়। মাঝে মাঝে, কোনও কোনও পরাবাস্তব দিনে—নিতান্ত অসম্ভব ঘটনাটিও ঘটে যায় টুপ করে। সেরকমই একদিন, এক অদ্ভুত শনিবারের দিনে—আমি তানিয়াপুর খোঁজ পাই।
রীতিমতো টেনেটুনে আমাকে জিমে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন ফারহানা। বাড়ন্ত ওজন এবং ভরভরন্ত ভুঁড়ির কারণে আচমকা একদিন হার্ট অ্যাটাক করে মরব—এই তার ভয়! কে জানত সেই জিম নামক বিশ্রী জায়গাটাতে এমন চমক লুকিয়ে ছিল? সেখানে আমার ট্রেইনার যিনি নিযুক্ত হলেন, তাঁর নাম মোহাম্মদ জহির হোসেন—আমাদের গোলবাগ স্কুলপাড়া বত্রিশ নাম্বার লাইনের সেই বডিবিল্ডার জহির ভাই! আমাকে চিনতে পেরেই হো হো করে হেসে বললেন, “সেদিনের সেই প্যাকাটি ছেলেটার আজ ভুঁড়ি বেরিয়ে গেল! কালে কালে কত কী দেখব!”
ফারহানা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। অন্তত পূর্বপরিচিত ট্রেইনারের আকর্ষণেও যদি স্বামীরত্নটি নিয়মিত জিমে আসে—সেও ঢের!
আমি প্রচণ্ড রকমের অবাক হলাম। গোলবাগ ছেড়ে জহির ভাই রামপুরায় কবে এলেন! জিজ্ঞেস করতেই দ্বিতীয় চমকপ্রদ খবরটি শুনলাম। নিতান্ত নতুন প্রেমিকটির মতোন একরাশ লজ্জা মাখা মুখ নিয়ে জহির ভাই ফিসফিস করে বললেন, “এখানেও বোধহয় থাকা হবে না রে বেশিদিন! তানিয়া টের পেয়ে গেছে আবারও—”
গুনে গুনে তিনটি হার্টবিট মিস হয়ে গেল আমার। অথচ, হার্ট ফেইলিউর থেকে বাঁচাবে বলেই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে ফারহানা—irony আর কাকে বলে!
ঘটনা যা শুনলাম সেটা এরকম—
আমরা হারিয়ে ফেললেও এই এতগুলি বছর ধরে একটি দিনের জন্যেও তানিয়াপুকে হারাতে দেননি জহির ভাই। গোলবাগ থেকে যশোর, তারপর সিলেট, উত্তরা, ধানমন্ডি এবং সবশেষে রামপুরা— জহির ভাইয়ের লগবুক। এই অদ্ভুত রুটে জীবন চালানোর কারণ হচ্ছে— তানিয়াপু। যশোরে পড়ালেখার পাট চুকিয়ে তানিয়াপু ভর্তি হয়েছিলেন সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে, এরপর উত্তরা একট মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জয়েন করেন। এর মধ্যে বার চারেক তানিয়াপুকে অফিসিয়াল এবং আনঅফিসিয়াল—দুইভাবেই ‘প্রপোজ’ করে ফেলেছিলেন জহির ভাই। “করুণার প্রয়োজন নেই”—বলে প্রতিবারই ফিরিয়ে দিয়েছেন তানিয়াপু। জহির নামক ফেউ-টিকে পিছু ছাড়াবার জন্যেই দুইবার চাকরি পর্যন্ত বদল করেছেন—লাভের লাভ কিছুই হয়নি। বর্তমানে যে জিমটায় জহির ভাই ট্রেইনার হিসেবে আছেন, একটা বহুতল শপিং কমপ্লেক্সের পঞ্চম তলায় সেটি। ঠিক মুখোমুখি বাড়িটার পাঁচতলাতেই তানিয়াপু থাকেন। জহির ভাইয়ের মাত্রাতিরিক্ত উকিঝুঁকির ফলাফলস্বরূপ তানিয়াপু এবারেও জেনে গেছেন, ফেউ আজও পিছু ছাড়েনি। অতএব, রামপুরার পাঠও যেকোনও দিন চুকে গেল বলে!
আকস্মিক একটা কথা মনে পড়ল আমার। জহির ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, “কিন্তু, আপনি তো সেই একটা মাত্র চিঠি দিয়ে আর কোনো যোগাযোগই রাখেননি তানিয়াপুর সাথে! কতজন তো প্রতিদিন চিঠি দিতো—”
“যখন জানলাম, ক্লাস এইটে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে তানিয়া—আমি বুঝলাম, ও মেয়ের আমি যোগ্যই নই! পড়ালেখার নাম শুনলে জ্বর আসে আমার, ওর পাশে মানাতো আমাকে? তাই সরে গিয়েছিলাম—”, জহির ভাই বলেছিলেন, চোখভর্তি দুঃখ নিয়ে। তারপর বলেছিলেন, “টেনেটুনে বি.এ পাশ করেছি। ওর যোগ্য আমি এখনও নই রে মুহিব! তবে এইটুকু জানি, আমার মতোন করে ওকে কেউ ভালবাসতে পারবে না কোনোদিন। কেবল ভালবাসাটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই আমার কাছে। সেটুকুর দাবিতেই আজও পিছে পড়ে আছি রে!”
সেই ষোল বছরের মুহিবের প্রশ্নের উত্তর পেল এই তিরিশের মুহিব। জানলো—সত্যিকারের ভালবাসায় স্বার্থ থাকে না, যুক্তি থাকে না; যা থাকে তার পুরোটাই ভালবাসা। সেই ভালবাসার সন্ধান যে পেয়েছে সে জানে—নিজেকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়ে কী করে ভালবাসার মানুষটিকে আলোকিত করে রাখা যায়!
আমরা কথা বলছিলাম রিসেপশন রুমে। ফারহানা এতক্ষণ বসে ছিল চুপচাপ। কোথা থেকে কী হলো কে জানে, ধুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বলল, “তুমি যাবে আমার সাথে?”
স্ত্রী হবার আগে, এই মেয়েটা আমার বন্ধু ছিল। তানিয়াপুর ঘটনার আদ্যোপান্ত আমি নিজেই তাকে বলেছিলাম। বহুবার সে আমাকে বলেছে, “আমি প্রতিদিন নামাজে দোয়া করি, তোমার তানিয়াপুর কাছে অন্তত একবার ক্ষমা চাইবার সুযোগ যেন আল্লাহ তোমাকে দেন!”
তাই, ফারহানা কোথায় যাবার কথা বলছে, সেটি বুঝতে আমায় বেগ পেতে হলো না।
জহির ভাইকে টেনেটুনেও নেওয়া গেল না। তানিয়াপুর সামনে কিছুতেই তিনি আর যাবেন না। দূর থেকে ভালোবেসে যাওয়াতেই নাকি তাঁর আনন্দ! অতএব, ফারহানার সঙ্গী হলাম কেবল আমি।
পরিশিষ্টঃ
ঠিক এক মাসের মাথায় তানিয়াপু আর জহির ভাইয়ের বিয়েটা সেরে ফেলা হয়েছিল। পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর হাসিটা আমি সেদিন দেখেছিলাম বর-বউয়ের মুখে। ফাইয়াজকে কোলে করে ফারহানা পুরোটা সময় ওদের সাথে সাথেই ছিল। মাঝে একবার এসে শুধু বলে গিয়েছিল, “এমন ভালোবাসা সবার ভাগ্যে জোটে না! তোমার তানিয়াপুর কপাল বটে!”
আমি গম্ভীর মুখে বলেছিলাম, “সে কপাল তোমারও আছে!”
ফারহানা হেসে কুটিকুটি হয়েছিল। বলেছিল, “এক রবিবারে মরলে পরের রবিবারে আরেক বিয়ে করবে— তার আবার অত দম্ফাই!”
কথা বাড়াইনি। ভালোবাসার পরীক্ষায় হেরে যাবার অতীত ইতিহাস যার আছে, তার আর কথা বাড়ানো চলেও না!
যে অসাধ্য জহির ভাই পনের বছরেও সাধন করতে পারেননি, ফারহানা মেয়েটা যেন যাদুমন্ত্র বলে পনের দিনেই সেটা করে ফেলেছিল! টানা দুই সপ্তাহ বাড়িঘর ফেলে কেবল ফাইয়াজকে সাথে নিয়ে সে পড়ে ছিল তানিয়াপুর কাছে। কী বলেছে, কী বুঝিয়েছে—আমি তার কিচ্ছু জানি না, জানবার চেষ্টাও করিনি। তবে আন্দাজ করতে পারি কিছুটা। কলেজ লাইফে ফারহানা ছিল তুখোড় বিতার্কিক। আমি নিশ্চিত, মাথামোটা জহির ভাই পনের বছরের চেষ্টাতেও যে তীব্র ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে পারেননি ঠিকঠাক, যুক্তি-তর্কের লেজুড় ধরে সেটাকেই টেনে বার করেছে ফারহানা, একেবারে ব্যবচ্ছেদসমেত দেখিয়েছে তানিয়াপুকে।
করুণা, ভালোবাসা আর ঘৃণা—একই মালার তিনরঙা তিনটে পুঁতি। রঙগুলির পার্থক্য খুব সামান্য, সকলের চোখে ধরা পড়ে না। ভাগ্যিস, ফারহানার সেই চোখ ছিল! নইলে, মধ্যবয়সে এসে কৈশোরের অজানিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি কেমন করে করতাম?
★
গল্প- ভালোবাসা বৃত্তান্ত