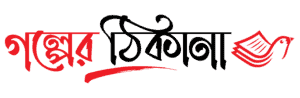-‘সাঁঝক বাতি-‘
নূরজাহান আক্তার (আলো)
[১১]
বেশ কিছুদিন পর,
আজ শুক্রবার! এখন বিকেল পাঁচটা। ছুটিরদিন তাই সবাই বাসাতেই আছে। সারাদিন পরিবারের সঙ্গে বেশ ভালো সময় কেটেছে। দুপুরে ভরপেট
খেয়ে অনেকে ভাতঘুমও দিয়েছে। দিগন্ত নিজেও ঘুমায় নি শিফাকেও ঘুমাতে দেয় নি। সে এখন
কানে ইয়ারফোন গুঁজে শুয়ে আছে। মুখে কালো রংয়ের ফেসপ্যাক লাগানো। নামিদামি ব্র্যান্ডের।
ব্র্যান্ডের জিনিস ছাড়া তার চলে না। তাছাড়া সে
ফেস নিয়ে খুব সতর্ক। ব্যস্ত থাকলেও হেলা করে না। শিফা সোফাতে বসে টিভিতে নাটক দেখছে। হিন্দি সিরিয়ালের প্রতি আগ্রহ নেই। মাঝে মাঝে
একটু-আধটু বাংলা নাটক আর সংবাদ দেখে, এই যা। সাফা থাকতে হরর মুভি দেখা, ড্রাইভিং,
বাজি ধরে খাওয়া, সাইকেল চালানো, ক্যারাতের প্র্যাকটিস, এসব ওদের নিত্যদিনের কাজ ছিল।
সাফা নেই। তাই এসব আর করা হয়েও ওঠে না। আনন্দগুলো যেন জীবন থেকে সব মুছে গেছে। এখন রঙহীন জীবন! তবুও তো বেঁচে আছে, এই ঢের। শিফা সাফার ছবির দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। লজ্জাও করে তাকাতে; হেরে গেছে। উদ্দেশ্যেও অসফল! পরিকল্পনাও বৃথা।
পরিশেষে পরাজিত এক মানবী। আপনজনদের
বিপদমুক্ত করতেও ব্যর্থ। ওর জন্য সবার জীবন
ঝুঁকিতে। একারণে সাফার ছবির দিকে তাকায়ও না। ওর মনে হয় সাফা বলছে,’ তুইও হেরে গেলি শিফা! আমার বিশ্বাসও ভেঙে দিলি!’
একজন মানুষ সবাইকে ভালো রাখতে পারে না।
কেউ না কেউ বেজার থাকেই। তেমনি সেও পারে নি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে হয় নি। এসব ভেবে
শিফা বেলকণিতে গিয়ে দাঁড়াতেই দিগন্ত ডাকল।
ওর ডাক শুনে মনে হচ্ছে খুব জুরুরি কিছু।শিফা নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াতেই দিগন্ত ওর ফোন এগিয়ে দিয়ে বলল,
-‘দেখো, মেয়েটা হাত কেটে পাশের ওই ছেলেটার নাম লিখেছে। তুমিও লিখো, প্লিজ!’
-‘সকালে আপনার ফোন হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। এজন্য এই শাস্তিটা, তাই না?’
-‘বাপ্রে, বুঝলে কিভাবে?’
শিফা হাসল! সকালে তাড়াহুড়োয় কিছু বলেনি। তাই শোধ নিচ্ছে। ফোনটা ওর হাত ফসকে পড়ে গিয়েছিল। ফোনের স্কিণ কিছুটা ফেটেছে। শিফা
ইচ্ছে করে করে নি দিগন্তও জানে, তবুও! হয়তো
এটা শাস্তি দেওয়ার ছুতো মাত্র। দিগন্ত মুখ ধুয়ে আগে ফ্রেশ হয়ে আসল। তারপর শিফাকে ওর সামনে বসিয়ে পটাপট দু’টো ইনজেকশন পুশ করল। অবশের ইনজেকশন! শিফা নিশ্চুপ হয়ে দিগন্তের হাসিটা দেখছে। ফিচেল হাসি! প্রানবন্ত
লাগছে। দিগন্ত খুব আগ্রহ নিয়ে কাজটা করছে।
যেন এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পূর্ণের কাজ।
দিগন্ত উঠে একটা বক্স আনল। সবুজ রংয়ের।
সেখানে ডাক্তারদের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি আছে। এক একটা যন্ত্র এক এক কাজের। দেখে মনে হচ্ছে সদ্য কেনা। দিগন্ত হেসে শিফার হাতে ওর নাম লিখতে থাকল। টপটপ করে লাল রক্ত ঝরছে৷ রক্তে বেডশীট ভিজে যাচ্ছে। এখন বিশ্রী দেখাচ্ছে সুন্দর বেডশীটটা। দিগন্তের হাত থেমে নেই। সে নিজের কাজে মগ্ন। শিফা দু’চোখ বন্ধ করে বসে আছে। হাত অবশ করাতে কিছু বুঝতে পারছে না। তবে গভীরভাবে দিগন্ত নাম লিখছে, তা বুঝতে পারছে। শিফা কাঁদতে চাচ্ছে না।তবুও চোখ বারণ শুনছে না। অঝরে অশ্রু ঝরিয়েই যাচ্ছে। দিগন্ত লিখা শেষ করে হাত ব্যান্ডেজ করে হাসল। আহা! এখন শান্তি লাগছে। শিফা থম মেরে বসে আছে। নিজেকে মস্তিষ্কশূন্য লাগছে।
একটুপরে, শিফা দু’চোখ খুলে হাত দেখে হাসল। ভুলের শাস্তি! শিফা চোখ মুছে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকল। আর দিগন্ত শিষ বাজাতে বাজাতে চলে গেল।
শিফা রক্ত রাঙানো বেডশীটটার দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়ল। মাথাও ঘুরছে। অবশ ছুটছে হয়তো, ব্যথা বাড়ছে। চিনচিনে অসহ্য ব্যথা। দিগন্তকে আসতে দেখে শিফা চোখ বন্ধ করে নিলো। সহ্য হচ্ছে না এই যন্ত্রণা। না বুকের আর না হাতের।
চারিদিকে মাগরিবের আজান দিচ্ছে। আজানের
সুমধুর সুর ভেসে আসছে। প্রাণ জুড়ানো সুর।
শিফাকে শুতে দেখেও দিগন্ত কিছু বলল না। সে
নিজের মতো রেডি হয়ে বেরিয়ে গেল। একটুপরে, নিহা এসে শিফাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। ওর নামে পার্সেল এসেছে। বড় পার্সেল! শিফার হাতে
ব্যান্জেজ দেখে নিহাসহ সবাই জিজ্ঞাসাও করল।
শিফা কথা এড়িয়ে পার্সেলটা নিয়ে ড্রয়িংরুমেই খুলতে বসল। অবাক হলেও সেটা প্রকাশ করল না। দিগন্ত বাদে এখানে সবাই উপস্থিত আছেন। সবার উৎসুক দৃষ্টি। শিফা পার্সেল খুলেই দুই পা পিছিয়ে গেল। ভয়ার্ত চাহনি। ওর পুরো শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। শিফার অবস্থা দেখে নিহা দ্রুত ধরে বসাল। দৌড়ে পানি এনে খাওয়াল।
দিগন্তের বাবা কিছু বুঝতে না পেরে পার্সেলের দিকে তাকালেন। দেখে, উনিও চমকে উঠলেন।
পার্সেলের মধ্যে কঙ্কাল। তবে মনে হচ্ছে, কারো কঙ্কালের পুরো বডি’ই পার্সেল করা হয়েছে। এটা উপহার। তাও আবার কঙ্কাল! কে এমন ভয়ানক চিন্তা-ধারার মানুষ? উনিও শিফাকে কিছু বলার শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না। কারণ সবাই’ই হতবাক।
একটু সময় নিয়ে শিফা নিজেকে সামলে নিলো।
সে উঠে পার্সেল খুলে আবার দেখল। পার্সেলের
মধ্যে কালো রংয়ের চিরকুটও আছে। তনয়ের বেলাতে যেরকম দিয়েছিল। তাহলে সেই ব্যাক্তি।
শিফা কাঁপা হাতে চিরকুট খুলে দেখে,
-‘নাও, তোমার স্বপ্নীলকে ফেরত দিলাম। তেমন কিছু করি নি। শুধু এডিসের কূপে ছেড়ে হালকা করে ভেজেছি। যদি স্বপ্নীলের কঙ্কাল বিশ্বাস না হয়, তাহলে অপেক্ষা করো। দুইদিন পর, তোমার ছোট ভাই রাফিটাও পেয়ে যাবে। জানো? আমি মানুষ ভাজতে বেশ পটু।’
এইটুকুই পড়ে শিফা ধপ করে বসে পড়ল। শরীর যেন অকেজো হয়ে গেছে। কেউ যেন শরীরের সব শক্তি শুষে নিয়েছে। বিচারবুদ্ধির লোপ পেয়েছে। আর কত সহ্য করবে? কত? আর কতজনকেই বা হারাবে? কষ্টে যে বুকটা ঝাঁজরা হয়ে যাচ্ছে।
শিফা মাথা নিচু করে থম মেরে বসে রইল। কথা বলছে না, অশ্রুও ঝরাচ্ছে না। সে নিষ্প্রাণ দেহে পার্সেলের দিকেই তাকিয়ে রইল। তখন প্রশান্ত শিফাকে বলল,
-‘শিফা! এ্যাই শিফা! বোন আমার কিছু হয় নি।
কেউ হয়তো মজা করে দিয়েছে। ভয় পেও না।’
দিগন্তের মা শিফার মাথায় পিঠে স্নেহের হাত বুলিয়ে বললেন,
-‘মারে, আমার সবাই আছি। ভয় পাস না মা।’
নিহা কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলছে। সে এসবে খুব ভয় পায়। একবার তো কঙ্কালের হরর মুভি দেখে জ্বর এসেছিল। সেই জ্বরটা একসপ্তাহ ছিল। পরে তাবিজ কবজ করে জ্বরটা সেরেছিল। ওই জ্বরের কথা ওর এখনো মনে আছে। যদিও ভোলার মতোও না। নিহা দ্রুত উঠে প্রশান্তের গা ঘেষে দাঁড়াল। স্বামী’ই আপন। স্বামীর কাছে বউ নিরাপদ। বাহ্, এই যে এখন আর ভয়ও লাগছে না। এসব ভেবে নিহা মনে মনে হাসল।
দিগন্তের বাবা-মা শিফাকে বুঝ দিচ্ছে। প্রশান্তও চেষ্টা করছে। মেয়েটা সত্যিই ভয় পেয়েছে। এমন করার মানে হয়? শিফা নিশ্চুপ হয়ে সোজা রুমে চলে গেল। যে ভয়টা পাচ্ছিল তাই হলো। এখন সে বেঁচে থেকে কি করবে? পরাজয় মেনেও কাজ হলো না। ওর জন্যই এতকিছু। শিফা স্বপ্নীলকেও বাঁচাতে পারল না। পরিশেষে, স্বপ্নীলও নিঃশেষ।
ওর হারানোর লিষ্ট কবে পরিপূর্ণ হবে? কবেই বা কিঞ্চিৎ শান্তি মিলবে? যাদের ভালোর জন্য সে নিজেকে বদলাতে চাচ্ছে; তারাই তো থাকছে না।
ওদিকে, দিগন্তের পরিবারও কিছু বুঝতে পারছে না। এসবের মানে কী? আর শিফাকে এসব কে পাঠালো? চিরকুটে কী লিখা ছিল? শুধু কঙ্কাল দেখে ভয় পাচ্ছে নাকি অন্যকিছু? হলেও কারণ কি? উনার আর কিছু ভেবে পাচ্ছেন না। শিফা ততক্ষণে রুমে দরজা আটকে দিয়েছে। কোনো সাড়াশব্দও নেই। নিহা আর শাশুড়ি অনবরত ডেকে যাচ্ছে। শিফা জবাব দিচ্ছে না। মেয়েটা ভুল-ভাল কিছু করে বসবে না তো? আত্মহত্যা
বা ভুল পদক্ষেপ। উনারা এসব ভেবে ঘাবড়েও
যাচ্ছেন। তাই কালবিলম্ব না করে দ্রুত দিগন্তকে ফোন দিলেন। পুরো ঘটনার সারমর্ম জানালেন।
দিগন্ত বাসার আশেপাশেই ছিল বিধায় চলেও এলো। যদিও আসার ইচ্ছে ছিল না। সে জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া সবাইকে বোঝাতে হবে শিফা তার সবকিছু। বউ ছাড়া তার পুরো জীবন অচল। ওর ভালোবাসায় খাদ নেই। ভালোবাসে বলেই; হাত কেটে নাম লিখতে বিবেকে বাঁধে নি, কষ্টও হয় নি। দিগন্ত এসে দরজা ধাক্কিয়েও ব্যর্থ হলো। রাগে ওর পুরো শরীর জ্বলছে। বেয়াদবটা আবার নখরা শুরু করেছে। বিকেলের শাস্তিটা বোধহয় কম হয়ে গেছে। ডোজ’টা বাড়াতে হবে।
দিগন্ত রাগটা সামলে লক ভাঙ্গার ব্যবস্থা করল।
তাছাড়া হবে না। মিস্ত্রি এসে লক ভেঙ্গে ফেলল।
কিন্তু শিফাকে পেল না। সে রুমে’ই নেই। বাসার সবাই অবাকের চরম শিখরে। মেয়েটা কোথায় গেল? দরজা আটকানো ছিল, তাহলে? এভাবে যাওয়ার মানে কি? আর গেল’ই বা কিভাবে?
দিগন্ত বেলকনিতে গিয়ে দেখে রেলিংয়ে ওড়না বাঁধা। ব্যাপারটা বুঝতে বাকি নেই। সবার চলে গেলে দিগন্ত শব্দ করে হাসল। আহারে, বেচারা শিফা! ভয় পেয়ে অবশেষে পালিয়েই গেল। তবে দিগন্ত জানে শিফা থেমে যাওয়ার পাত্রী নয়। সে ঠান্ডা মস্তিষ্কের মেয়ে। ঝোপ বুঝে কোপ মারবেই, মারবে। শিফা এতদিন দুঃখীর অভিনয় করেছে।
মেয়েটা প্রচুর ধূর্ত। আর অভিনয় করতে করতেই পাতাল ঘরের সন্ধান পেয়ে গেছে। ভালো সেজে দিগন্তের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করেছিল।
সেও জানত, দিগন্তের নজর সর্বদা ওর দিকেই।
তবে দিগন্তকে ফাঁকি দেওয়াও এত সোজা নয়।
সে ঠিকই ধরে ফেলেছে। দিগন্ত হাসতে হাসতেই বলল,
-‘খুব শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে, জান। মারতে নয়তো মরতে।’-‘সাঁঝক বাতি-‘
নূরজাহান আক্তার (আলো)
[১২]
ঢাকায় দশতলা বিশিষ্ট রয়েল হসপিটাল। বেশ উন্নত। চিকিৎসার মানও বেশ ভালো। বিলাশ বহুল হসপিটালটা অসহায় এবং গরীবদের জন্য নয়। কারণ তারা খরচ বহন করতে অক্ষম। এই
হসপিটালের মালিক সাজ্জাদ হোসাইন শখ করে তৈরী করেছিলেন।অসহায়দের মানুষের চিকিৎসা প্রদানের জন্য। উনি ছিলেন নিঃসন্তান। অঢেল সম্পত্তির মালিকও। দেশের সব সম্পত্তি ভাইয়ের ছেলেদের দিয়ে প্যারাগুয়েতে চলে গিয়েছিলেন।
আর এই হসপিটালের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, বন্ধু
সুমন শেখকে। বাল্যকালের বিশ্বস্ত বন্ধু। সুমনের দুই ছেলে প্রশান্ত ও দিগন্ত। সুমনের বড় ব্যবসাও আছে। প্রশান্ত পড়াশোনা শেষ করে বসেই ছিল।
তার ভাবনা, কিছুদিন পর বাবার সঙ্গে ব্যবসাতে যোগ দিবে। ততদিনে একটু নিজেকে সময় দিবে।
ব্যবসাতে ঢুকে গেলে দিন দিন ব্যস্ততাও বাড়বে।
তখন চাইলেও আর এই সময়টা ফিরে পাবে না।
কিন্তু সাজ্জাদ প্রশান্তকে খুবই পছন্দ করেছিলেন। ওর মতো দায়িত্ববান ছেলেকে উনি খুঁজছিলেন।
প্রশান্তর সঙ্গে কথা বলে, উনি হসপিটালের সব দায়িত্ব প্রশান্তকে দিলেন। দিন যায়, মাসও যায়।
সময় পেরিয়ে দিনও কাটতে থাকে। দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে প্রশান্তেরও ব্যস্ততা বাড়তে থাকে। সে তার দায়িত্বে অটল। সেবার মান ভালো হওয়াতে ওর হসপিটালের নামও চারদিকে দ্রুত ছড়াতে থাকে। দিনকে-দিন হসপিটালটা উন্নত করার প্রচেষ্টাও চালাতে থাকে। তিনতলা হসপিটালে পেশেন্টের সুবিধায় আরো বড় করতে থাকে। ধীরে ধীরে তা দশ তলাতে ঠেকে। এর বছর চারেক পর সাজ্জাদ হোসাইন দেশে ফিরে এলেন। এবং হসপিটালটা উনার বোনের মেয়ের নামে করে দিতে চাইলেন।
তাহলে প্রশান্তও মুক্তি পাবে। কতদিনই বা ওকে
ধরে রাখবেন। ওর অন্যকিছু করার ইচ্ছে থাকতে পারে।
কিন্তু ততদিনে হসপিটালের উপরে প্রশান্তের মায়া জন্মে গেছে। এতদিনের পরিশ্রম। চার বছরে কম পরিশ্রম করে নি। নিজের ভেবেই হসপিটালটাকে এত বড় করেছে। প্রশান্তকে ভেঙে পড়তে দেখে, প্রশান্তর বাবা বন্ধু সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে কথা বললেন। এবং জানালেন হসপিটাল উনি কিনে নিবেন। কিন্তু সাজ্জাদ হোসেন তা মানলেন না। উনার বোনের একমাত্র মেয়ে শিফা। আর উনি শিফাকে খুব ভালোবাসেন। এই হসপিটাল উনি শিফাকে জন্মদিনে উপহার হিসেবে দিবেন। এটা উনি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন। উনাদের
বংশে শিফা বাদে কোনো মেয়ে নেই। এজন্য এত আদরের! নিঃসন্তান সাজ্জাদকে শিফা বাবা বলে ডাকত। শিফার মুখে প্রথম বাবা ডাক শুনে উনি কলিজা ঠান্ডা করেছিলেন। অনুভব করেছিলেন
এই ডাকের মায়া।তাই বন্ধুর কথা রাখতে পারেন নি। তাই বুঝিয়েও বলেছিলেন,
-‘সুমন, আমি সত্যিই দুঃখিত রে ভাই। শিফাকে
আমি খুব ভালোবাসি। ওটা আমার আরেকটা মা। আর শিফা মায়ের জন্য আমি হসপিটালটা রেখেছিলাম। কষ্ট নিস না বন্ধু।’
সুমন শেখ কষ্ট পেলেও জবাবে কিছু বলেন নি। ব্যাপারটা বুঝে চলেও এসেছিলেন। না পেলে কি আর করার। চেষ্টা তো করেছিলেন।এর কিছুদিন পর, সাজ্জাদ হোসাইন নিঁখোজ হলেন। কোথাও উনার খোঁজ মিলল না। এমনকি এখনো উনার লাশও না। তখন শিফা ভেঙে পড়েছিল। পরে,
পরিবারের সাপোর্টে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। সাজ্জাদ হোসাইন ছিলেন শিফার বন্ধু। তারপর মামা। সব আবদার উনার কাছেই। এমনকি, সে মামার কাছে জেদ ধরেই ক্যারাত শিখেছিল।ওর বাবা-মা রাজি হচ্ছিল। পরে মামার কথাতে মত দিয়েছিলেন। উনার নিঁখোজের আটমাস পর,
গোপন সূত্রে জানা গেছে, উনাকে কেউ এসিডের কূপে ফেলেছিল। এসিডে উনার শরীরটা ঝলসে
কঙ্কালে রুপান্তরিত হয়েছিল।
ওই ঘটনার একবছর পর,
বাবা- মা আর সাফা-স্বপ্নীল চার সদস্যের সুখী পরিবার। সুখ যেন পরিবারে উপড়ে পড়ত। ওরা এতটাই সুখে ছিল। শিফাদের নতুন বাড়ির কাজ চলছিল। এজন্য কিছুদিন ভাড়া থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যাতে বাড়ির কাজটা ধীরে সুস্থে হয়।
তাড়াহুড়োর কাজ ভালো হয় না। স্বপ্নীল বাইরের দেশে থাকে। উনারা মাত্র তিনজন। এতে সমস্যা হওয়ার কথা না। তাছাড়া মাত্রকয়েকটা মাসেরই ব্যাপার। খোঁজ নিয়ে, চারতলা বিশিষ্ট বাড়িটার নিচে তলায় ভাড়া এসেছিল। এই বাড়ির মালিক সুমন শেখ। খুব ভদ্র একজন মানুষ। এলাকাতে
ভলোই সুনাম রয়েছে। উনার ছেলে দু’টোও ভদ্র, প্রশান্ত ও দিগন্ত। দেখা হলে, আগে সালাম দেয়।
কত্ত সুন্দর তাদের বিনয়ী ব্যবহার। আর সেখানে ঝোট-ঝামেলা ছাড়া ভালোই দিন কাটছিল।
সাফা একমাত্র কলিজার বান্ধবী শিফা। দু’জনে যেন একে অন্যের প্রাণ। কলেজ জীবনে তাদের
বন্ধুত্বের সূচনা। সাফা সহজ সরল এবং নরম মনের। আর শিফা সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সর্বদা একটু কড়া টাইপের। ওই বাসার ছোট ছেলেটাকে সাফার খুব মনে ধরেছিল। লুকিয়ে দেখতোও।লজ্জায় লাল হয়ে একথা শিফাকে জানিয়েছিল।
শিফা ভ্রু কুঁচকে বলেছিল,
-‘আমি আগে দেখব ছেলেটা কেমন। তারপর..!
নয়তো বাদ।’
-‘আচ্ছা, তুই যা বলবি তাই!’
শিফা সাফারদের বাসায় ঘনঘন আসত। কিন্তু দিগন্তকে দেখত না। তবে মাঝে মাঝে প্রশান্তকে দেখত। একদিন ফুল ছেঁড়ার সময় দিগন্ত নিজে এসে কথা বলেছিল। তারপর থেকে শিফা ওকে ফলো করত। ছেলেটার উপর নজর রেখে তেমন কিছু পায় নি। বরং বেশ সুনাম রয়েছে। মেয়েলি কেস নেই। বাবা-মায়ের আদর্শ ছেলে। তারপর
শিফা খোঁজ নিয়ে সাফাকে বলেছিল,
-‘ তুই প্রেমে লেগে পড়। তোদের বিয়ের অবধি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার।’
সেদিন সাফার খুশির অন্ত ছিল না। শিফাকে যে কতবার জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল হিসাব নেই। তবে দিগন্তকে দেখলেই কাঁপুনি শুরু হয়ে যেতো। না কিছু বলতে পারত; না বলতে দিতো। দিগন্তকে সে প্রিয় বলতে ডাকত। একদিন সাফা এটাও বলেছিল, ‘তুই আমার সতীন হবি। আমরা এক সাথেই থাকব। আর বরকে নিয়ে ঝগড়া করব।’
শিফা ওর কথা শুনে রেগে গেলে সাফা খিলখিল করে হাসত। যদিও ইচ্ছে করেই শিফাকে রাগিয়ে দিতো। সাফা স্বপ্নীলকে নিয়েও শিফাকে খোঁচা মারত। ভাইয়ের বউ, আম্মুর পুত্রবধূ, সাফার ভাবি, এসব বলে প্রায় ডাকত। এসব খুনশুটিতে
মেতে থাকত। বেশকয়েকদিন পর, দিগন্তই আগে সাফাকে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠাল। সাফা
কালবিলম্ব না করে কনফমও করে ফেলেছে। সে
যেন আকাশের চাঁদ পেয়েছে। তারপরে দু’জনের
টুকটাক কথাও হতো। দিনকে-দিন সম্পর্কটাও
সহজ হতে লাগল। কতশত প্রেমালাপও চলত।
দিগন্ত মর্জিমতো সাফাকে ছবি দিতে বলত। না দিলে কথা বলত না, এড়িয়ে চলত। সাফা ওর এড়িয়ে চলা সহ্য করতে না পেরে ছবিও দিতো। তবে এসব কথা শিফাকে জানাত না। কারণ সে জানে, শিফা রাগ করবে। প্রিয় মানুষকেই দিচ্ছে,
তাহলে সমস্যা কোথায়? এভাবে সময় পেরেতো লাগল।
সাফা দিগন্তদের বাসাতেও যাওয়ার-আসা শুরু করল। নিহার সঙ্গে ওর আড্ডাও বেশ জমতো।
শিফাকে কম সময় দিতে লাগল। কষ্ট পেলেও শিফা কিছু বলত না। সে যতটুকু পারত, সাফার খোঁজ রাখত। সাফা পড়াশোনাতে অমনোযোগী
হয়ে গেল। তার কাজ, সারাদিন ফোনে দিগন্তের সঙ্গে চ্যাট করা। শিফা কিছু বললে উল্টে রাগ দেখাত। এরপরে হঠাৎ, সাফার শরীরটা খারাপ হতে শুরু করল। দিন দিন পাগলামির মাত্রাও বেড়ে গেল। স্মৃতিশক্তি কমতে শুরু করল।চোখে কম দেখতে লাগত। তবুও সারাদিন ফোন নিয়েই পড়ে থাকত। অনলাইনে না দেখলে দিগন্ত নাকি রাগ করত। দিগন্ত যখন যা বলত তাই’ই করত। যত দিন কাটতে লাগল সাফার সমস্যাও বাড়তে লাগল। সে মাঝে মাঝে শিফাকেও চিনতে পারত না। ভুল বুঝে অনেক আঘাতও করেছে। খানিক পরেই; দেখে, বুঝে, জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতোও।
কিন্তু ডাক্তারের কাছে যেতে চাইত না। এর কারণ
পরে জানা গেছে, দিগন্তই নাকি ডাক্তার দেখাতে নিষেধ করেছে। সারাদিন ফোন টিপে তাই নাকি এমন হচ্ছে। আপনাআপনি সব ঠিক হয়ে যাবে।
সাফা তাই বিশ্বাস করেছে। শিফা একদিন জোর করে, ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। শিফার চোখ এড়িয়ে সে পালিয়েও এসেছিল।
একমাস পর, সাফার আরো করুণ অবস্থা হয়ে গেল। তবে ওর ফোনটা কোথাও পাওয়া যায় নি। সে নিজে নিজেই কীসব বিরবির করত। সাফার অবস্থা দেখে ওর বাবা-মাও ভেঙে পড়েছিলেন। স্বপ্নীলের পরীক্ষা চলছিল। তাই আসতেও পারে নি। বোনের চিন্তায় পাগলপ্রায় অবস্থা হয়েছিল।
আর শিফা মনটা শক্ত করে সবাইকে সামলেছে।
সাফা করুণ অবস্থাতে শিফা কত কেঁদেছে, কত মানত করেছে। যাতে সাফা আগের মতোই হয়ে যায়। তা হচ্ছিল না। বরং বিপরীতটাই হচ্ছিল।
আর শিফার সঙ্গে সাফার শেষ কথাটা ছিল,
-‘প্রিয় আমার প্রাণ নিলো রে। হ্যাঁ, ওই, ওই প্রিয় আমার প্রাণ নিয়েছে।’
শিফা সাফার পাগলামি থামাতে ব্যস্ত হয়েছিল।
তাই কথাটাতে গুরুত্ব দেয় নি। সাফাকে বুঝিয়ে রাতে ঘুম পাড়িয়েও এসেছিল। তারপরের দিনেই সাফা আত্মহত্যা করেছিল। এই ঘটনা এখানেই থেমে থাকে নি। সাফার বডি নিয়েও আরেকটা ঘটনারও সূচনা হয়েছিল। অনাকাঙ্ক্ষিত শক!
সাফার চিকিৎসা চলাকালীন একটা বন্ড সাইন করতে হয়েছিল। যাতে, হঠাৎ শিফার কিছু হয়ে গেলে হসপিটাল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা না হয়।
সেই পেপারটা পুরো না পড়ে সাফার বাবা সাইন করেছিলেন। পুরোটা পড়ার ধৈর্য্য তখন উনার ছিলো না। অথচ সেই পেপারের নিচের পেপারে
লিখা ছিল,
-‘পেশেন্টের মৃত্যুর পরপরই চোখ আর কিডনীটা হসপিটালে জমা দিতে হবে। সেটা কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই। না দিলে, হসপিটাল কতৃপক্ষ যে কোনো ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবে।’
To be continue…..!!
To be continue……..!!